জিন সাম্রাজ্যবাদ
“দ্য ইকোলজিস্ট পত্রিকায় খুব সুন্দর একটি কার্টুন ছাপা হয়েছিল যার হেডিং ছিল ইভল্যুশন অফ সায়েন্স। ছবিটা এরকম—দুটো পাশাপাশি ছবির একটাতে গ্যালিলিও, তাঁর সামনে পোপ দাঁড়িয়ে। পোপ গ্যালিলিওকে বলছেন যে, তুমি যদি চার্চের ডগমা না মানো তাহলে তোমাকে পুড়িয়ে মারব। পরের ছবিতে পোপের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কর্পোরেট বস,আর গ্যালিলিওরূপী পুশতাইকে সে বলছে যে, তুমি যদি কর্পোরেট ডগমা না মানো তাহলে তোমাকে মামলা করে সর্বস্বান্ত করে দেব। এই হাস্যকর অথচ ভয়ঙ্কর বিবর্তনটা বিজ্ঞানের কিন্তু হয়েছে।”
লিখেছেন অভ্র চক্রবর্তী
আমরা এই লেখায় জিন সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আলোচনা করব। এ নিয়ে বলতে গেলে একটু জীববিজ্ঞানের কচকচানি হয়তো এসে পড়বে। কিন্তু তা পুরোপুরি এড়িয়ে গোটা বিষয়টি বলা একটু মুশকিল। আমরা এইভাবে দেখতে পারি। মানুষের অর্থনৈতিক কাজের জন্যে যত রকমের উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা আরও যা যা ব্যবহৃত হয়,তাদের কিছু বিশেষ গুণের জন্যই তারা অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই গুণগুলি নিয়ন্ত্রণ করে এক বা একাধিক জিন। যেমন ল্যাংড়া আমের যে দারুণ স্বাদ, তা একাধিক জিন নিয়ন্ত্রণ করে। আবার সেদ্ধ করলে লম্বায় বেড়ে যাওয়া সুস্বাদু ও সুগন্ধী বাসমতি চালের সব বৈশিষ্ট্যও নিয়ন্ত্রণ করে একাধিক জিন। ফলত মানুষ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর নির্ভর করে তার এই যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটা গড়ে তুলেছে, কৃষি, পশুপালন বা বহু শিল্পের কাঁচামাল — এসবের উপর ভিত্তিকরে, সেই সমস্ত কিছুই আসলে এক বা একাধিক জিনের ফসল। আর তাই এই জিন একটা সম্পদ। যতদিন যাচ্ছে, এই জিনসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষ অবহিত হচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য সম্পদের মতন জিনসম্পদও পৃথিবীর সব দেশে সমানভাবে পাওয়া যায় না। কয়লা বা খনিজ তেলও এমন সম্পদ। সেগুলি যে দেশে বেশি থাকে, আমরা জানি সেইসব দেশ কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধে ভোগ করে। জিনসম্পদও তেমনই। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী ভ্যাভিলভ তাঁর বিখ্যাত গবেষণায় পৃথিবীর নয়টি অঞ্চলকে চিহ্নিত করেছিলেন, যেগুলিকে জিনসম্পদের উৎস বলা চলে। ভারত-সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন, ইরাক অঞ্চল; দক্ষিণ আমেরিকার চিলি ও আন্দিজ অঞ্চল; মেক্সিকো। পরবর্তীতে মার্কিন বিজ্ঞানী হারল্যান-এর গবেষণাতেও (১৯৭১) এই ব্যাপারটা প্রমাণিত হয়। মানুষ যতরকমের শস্য বা প্রাণী ব্যবহার করে, তার কতগুলো নির্দিষ্ট উৎসকেন্দ্র রয়েছে অর্থাৎ সেন্টার অফ অরিজিন। মানে জিনসম্পদ সারা পৃথিবী জুড়ে সমানভাবে ছড়িয়ে নেই। জিনসম্পদের সাথে খনিজ তেল বা কয়লার পার্থক্য রয়েছে। সেগুলি একান্তই প্রকৃতির দান। মানে, পৃথিবীর কোথায় খনিজ তেল বা কয়লা আছে, সে ব্যাপারে মানুষের কোনও হাতই নেই; তবে এগুলি উত্তোলনের প্রযুক্তি তার করায়ত্ত হতে পারে। জিনসম্পদ কিন্তু নিছক প্রকৃতির দান শুধু নয়। এখানে আসলে দুটো ব্যাপার রয়েছে। একটা হচ্ছে মানুষের চাষআবাদের সাথে সম্পর্কিত। আজ থেকে ১২,০০০ বছর আগে যখন মানুষ প্রথম চাষবাস শিখল, দেখা যাবে যেখানে যেখানে সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তার আশপাশের জঙ্গল থেকে চাষযোগ্য খাওয়ার উপযোগী ফসলের গাছ তারা তুলে এনে চাষআবাদ করেছে। সেখান থেকে যেগুলো ভালো জাতের গাছ, সেগুলো আলাদা করে চাষ করেছে। সেগুলোর মধ্যে থেকে আরও ভালো গাছগুলিকে আলাদা করেছে ও চাষ করেছে। এইভাবে মানুষের ব্যবহার্য বিশাল একটা জিনসম্পদ তৈরি হয়েছে। আরেকটা ব্যাপারে আসা যাক। এই যে ন’টা অঞ্চলের কথা বলা হল জিনসম্পদের উৎস হিসেবে, সেগুলি শেষ হিমযুগের সময়ে (আজ থেকে ১২০০০ বছর আগে) জমে যায়নি। কারণ এই অঞ্চলগুলি প্রত্যেকটিই তিরিশ ডিগ্রি উত্তর থেকে তিরিশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। ফলত এই অঞ্চলগুলিতে উদ্ভিদ ও প্রাণী অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাওয়ার কারণে হিমযুগের পরেও বেঁচেবর্তে রয়ে গিয়েছিল, বিপুল জীববৈচিত্র্য নিয়ে। এই যে দু’টি ব্যাপার, অর্থাৎ একদিকে প্রকৃতির কারণে আর একদিকে মানুষের বহু প্রজন্মের শ্রম — এই দু’টির কারণেই কিন্তু এই সমস্ত জিনসম্পদের উৎপত্তি। যেমন ধরুন, এরকমটা বলা হয়, ভারতে সবুজ বিপ্লবের আগে পর্যন্ত ধানের প্রায় এক লক্ষ রকমের জাত ছিল। এটা মনে করার কোনও কারণ নেই যে, এই এক লক্ষ জাতের ধানই প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যেত। বরং এটাই সত্যি যে, চাষিরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিভিন্ন জাতকে ‘পিওর লাইন সিলেকশন’ নামক একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করেছিল। বহু প্রজন্ম ধরে পরীক্ষিত হওয়ার কারণে ধানের এই জাতগুলো আশ্চর্য এমন অনেক গুণ পেয়েছিল যা আজও, অত্যাধুনিক জিন-প্রযুক্তি ব্যবহার করেও, আধুনিক কোনও ধানের মধ্যে আনা বেশ কঠিন কাজ হয়ে পড়েছে। যেমন ধরুন এমন ধানগাছ আছে যা দশ-বারো ফুট জল সহ্য করেও দিব্যি বেঁচে থাকে। এমন ধানগাছও আছে যার খরা সহ্য করার ক্ষমতা বাজরা গাছের সমান। সুগন্ধী ধানের কথা আমরা সকলেই জানি। তেমনই মুড়ির ধান, খইয়ের ধান এমন বিচিত্র সব ধান আছে। বহু ধান আছে যারা বিভিন্ন ধরণের রোগপোকা প্রতিরোধী। এইসমস্ত ধানগুলিই কিন্তু ভারতীয় কৃষকের বহু প্রজন্মের বহু বছরের —অন্তত পাঁচ-ছয় হাজার বছরের সাধনার ফলে উৎপন্ন হয়েছিল। এবং এই যে জিন সম্পদ, এর লোভে ইউরোপীয়রা বহুবার ভারতে এসেছে। যেমন আমরা জানি ভাস্কো দা গামা এসেছিল মশলার লোভে। এত বহুবিধ মশলা আমাদের দেশে পাওয়া যায় যে সেগুলিকেও আমরা জিনসম্পদ বলতে পারি। তবে প্রাচীন যুগের ইউরোপীয়দের এই অভিযানের একটা গুণগত তফাৎ কিন্তু হয়ে গেল যখন সবুজ বিপ্লব এল। সবুজ বিপ্লবের সময় আসলে তিন-চারটে বেঁটে ভ্যরাইটির ধানগাছ, অর্থাৎ যাদের বাড় একটা জায়গার গিয়ে বন্ধ হয়ে যায়, সেগুলিতে বেশি পরিমাণে রাসায়নিক সার দিলে অনেক বেশি ফলন দিতে পারবে —এরকম একটা দাবি করে, শুধু সেগুলির চাষই গোটা ভারত জুড়ে আরম্ভ হয়।
এখানে একটা মজার তথ্য দিতে চাই। কয়েক বছর আগে পাঞ্জাবে একটি সেমিনার হয়েছিল। সেখানে ড. অনিল সদগোপাল উপস্থিত ছিলেন। এই অনিল সদগোপাল, ভারতের সবুজ বিপ্লবের জনক যাঁকে বলা হয় সেই এম. এস. স্বামীনাথন এর ছাত্র। এম. এস. স্বামীনাথন পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে জিনতত্ত্বই পড়াতেন, উদ্ভিদ জিনতত্ত্ব। এই স্বামীনাথন ক্লাসে নাকি বলতেন যে, পাঞ্জাবে কৃষি এতটা শক্তিশালী হওয়ার কারণ পাঞ্জাবের গমের জিনবৈচিত্র্য (মনে রাখতে হবে এই সময়কাল সবুজ বিপ্লবের আগেই)। নানারকমের ভ্যরাইটির গম পাওয়া যায় এখানে। যে কারণে পাঞ্জাবের গমে পোকা অনেক কম লাগে ইত্যাদি ইত্যাদি। এবারে, সবুজ বিপ্লব যখন চলছে, তখন দুয়েকটা গমের ভ্যরাইটি গোটা পাঞ্জাবে বা গোটা দেশজুড়ে চাষ করা হচ্ছিল। তখন অন্যান্য ভ্যরাইটিগুলোর চাষ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং সেগুলো অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। তখন এই অনিল সদগোপাল তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, “স্যার আপনিই তো বলেছিলেন যে, পাঞ্জাবে কৃষির মূল শক্তি তার শস্যের এই জেনেটিক ডাইভার্সিটি। তাহলে আপনিই এখন এমন একটা পদ্ধতি কেন চালু করছেন যাতে এই জেনেটিক ডাইভার্সিটিটা নষ্ট হয়ে যায়?” তখন স্বামীনাথন তাঁকে বলেন, সব প্রশ্নের উত্তর চেয়ো না। এরকম অনেক অনেক প্রশ্নের উত্তর তিনি যেমন অনিল সদগোপালকেও দেননি, তেমনই সারা ভারতের মানুষকেও দেননি। তাইচুং নেটিভ, আইআরএইট এইরকমের ধানের চাষ যখন দেশজুড়ে অবাধে করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে, তখন কটক সেন্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইন্সটিট্যুট-এর ডিরেক্টর ড. আর.এইচ. রিচারিয়া, খুবই বড় একজন কৃষি বিজ্ঞানী, একটি নির্দোষ বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি জানতে চান, “এইসমস্ত ধান, যেগুলি গোটা দেশজুড়ে চাষ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে, সেগুলির কোনও কোয়ারেন্টাইন সার্টিফিকেট নেই কেন?” কোয়ারেন্টাইন সার্টিফিকেট ব্যাপারটা এইরকম। আমি যখন বিদেশি কোনও উদ্ভিদ বা প্রাণীর যেকোনও ভ্যরাইটি আমার দেশে আনব, তখন আমার দেশের রোগপোকা, আবহাওয়া ইত্যাদির প্রতি সে কতটা সংবেদনশীল সেটা একটা বিচ্ছিন্ন জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে তাদের রেখে পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হবে। তারপর সন্তোষজনক ফলাফল মিললে তবে তাকে দেশে অবাধে চাষের জন্যে ছাড়পত্র দেওয়া হবে। এইরকম একটি নির্দোষ বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করার ‘অপরাধ’-এ তাঁর চাকরি চলে যায়। এক সুন্দর সকালে তিনি অফিসে গিয়ে দেখেন তাঁর চেম্বারটি সিল করা হয়ে গেছে। এবং তাঁর হাতে চাকরি থেকে বরখাস্তের কাগজ ধরিয়ে দেওয়া হয়। ওই চেম্বারের মধ্যে রয়ে যাওয়া তাঁর প্রচুর গবেষণাপত্র এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য তিনি ফেরৎ পেতে চান। তাঁকে দেওয়া হয় না। সেই সময়ের একটি সাপ্তাহিক ইলাস্ট্রেটেড উইকলি-তে প্রকাশিত ক্লদ আলভারেজ-এর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ ‘দ্য গ্রেট জিন রবারি’ তে এই ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। এরপর রিচারিয়া কটক সেন্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইন্সটিট্যুট-এর ডিরেক্টরের পদ খুইয়ে মধ্যপ্রদেশের ধান গবেষণা কেন্দ্রে একজন জুনিয়র সায়েন্টিস্ট হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন ধানের ভ্যরাইটি নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন। আমরা যারা ধানের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণের কাজে যুক্ত আছি তাঁদের কাছে এটা বিস্ময়ের যে তিনি তারপরে দেশি ধানের প্রায় ৬৫,০০০ জাত লিপিবদ্ধ করেন। ১৯৭১ থেকে ৭৬ সালের মধ্যে রিচারিয়া কেবল মধ্যপ্রদেশ থেকেই ১৯০০০ দেশীয় জাতের ধান সংগ্রহ করেছিলেন এবং তাদের গুণাগুণ বৈজ্ঞানিক ভাবে নথিভুক্ত করেছিলেন। সেখানে কাজ করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন, এমন অনেক দেশি ধানের ভ্যরাইটি আছে যেগুলোর চাষ দেশীয় পদ্ধতিতে, কোনওরকম কেমিক্যাল ইনপুট বাদ দিয়েও যদি করা হয়, তাহলে তারা আইআরএইট এর থেকেও বেশি ফলন দিতে সক্ষম। এরকম দুটি ধানের ভ্যরাইটির নাম আমার এখন মনে পড়ছে—মোকোদো আর চিনার। দি ইকোলজিস্ট পত্রিকায় ভরত ডোগরা-র লেখা থেকে এই তথ্য আমি পেয়েছি। পরে আমি ইথোলজিস্ট রতনলাল ব্রহ্মচারীকেও ব্যক্তিগত যোগাযোগের সূত্রে এটা জিজ্ঞেস করি যে, এরকম ধানের জাত আদৌ থাকতে পারে কিনা। তখনও আমি এই দেশি ধান নিয়ে কাজ আরম্ভ করিনি। আমার মনে প্রচুর সংশয় ছিল। কারণ বারবার মনে হচ্ছিল, এরকমের দেশীয় ধানের জাত যদি থাকবেই তাহলে এত ঘটা করে গ্রিন রেভুলেশন করা হল কেন! উনি বলেছিলেন এটা সত্যি। এরকম জাত সত্যিই আছে। সম্প্রতি আমি রিচারিয়ার একটি গবেষণাপত্র পড়ার সুযোগ পেলাম যেটি ১৯৭৭ সালে Madhya Pradesh Rice Research Institute থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে দেখলাম ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ভারতের মধ্যপ্রদেশে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, সেখানকার দেশীয় ধানের অন্তত আট শতাংশকে উচ্চফলনশীল বলে চিহ্নিত করা যায়, এদের গড় ফলন ছিল প্রতি হেক্টরে ৩.৭ টন বা তার বেশি, রিচারিয়া মধ্যপ্রদেশের (অধুনা ছত্তিশগড়) কৃষকদের তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে দেশীয় ধানের চাষ করে ভালো ফলন পেতে দেখেছেন, সেখানকার একটি জাতের ফলন হেক্টরে ৯ টনেরও বেশি ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় কৃষি বিজ্ঞানী সুজিত কুমার দে দত্ত সঠিক মাত্রায় রাসায়নিক সার ও জল সেচ করে আইআর এইট এর ফলন পেয়েছিলেন হেক্টরে ৯.৪ টন এবং ১৯৯৬ এবং ১৯৯৮ সালে আন্তর্জাতিক ধান গবেষনা কেন্দ্রে আইআর সিক্সটিফোর এর ফলন হয়েছিল বোরো ও খরিফ মরশুমে যথাক্রমে ৮.৭৬ ও ৮.২৮ টন প্রতি হেক্টর। আর আইআর সেভেন্টিটু এর ফলন হয়েছিল ৯.৫ ও ৯.০৬ টন প্রতি হেক্টর। আইআর সেভেন্টিটু হল আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রের তৈরি করা সর্বোচ্চ ফলনশীল আর আইআর সিক্সটিফোর সর্বাপেক্ষা বহুল প্রচারিত ধান। এবারে চিন্তা করে দেখুন, লক্ষ কোটি টাকা খরচা করে যেখানে সবুজ বিপ্লবের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, যার জন্যে নর্ম্যান বরল্যাগ-কে নোবেল শান্তি পুরস্কারও দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী বলছেন যে এমন দেশীয় জাত আছে যা আইআরএইট-এর থেকে বেশি ফলন দিতে পারে। এটা হজম করে নেওয়া খুব মুশকিল।
আর ঠিক এই সময়েই সমান্তরালভাবে কয়েকটি ঘটনা ঘটল। প্রথমত, ফিলিপিন্সে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইন্সটিট্যুট (IRRI) রিচারিয়া-কে একটি প্রস্তাব পাঠায় যে, আসুন আমরা আমাদের ধানের ভ্যারাইটির সংগ্রহ বিনিময় করি। মানে আপনার কাছে যা জার্মপ্লাজম সংগৃহীত রয়েছে তা আমাদের দিন, আর আমরা আমাদের সংগ্রহ আপনাকে দেব। রিচারিয়া সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, প্রথম কথা আপনাদের সংগ্রহটি এই দেশে আনলে তা বিপুলমাত্রায় রোগভোগে ও পোকায় আক্রান্ত হবে এবং তার থেকে আমার সংগ্রহে সংক্রমণ ছড়িয়ে গিয়ে আমার ভ্যরাইটিগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় কথা, আমার যে এই বিপুল সংগ্রহ, তা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা প্রথম আমি করব। বস্তুত এটা খুব স্বাভাবিক দাবি। আর তাই আমি আপনাদের সাথে জার্মপ্লাজম বিনিময় করতে আগ্রহী নই। দ্বিতীয়ত, এই ঘটনার পরে পরেই ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক থেকে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সরকারকে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেটা মধ্যপ্রদেশের চাষিদের কম সুদে ঋণ দেওয়ার একটি প্রস্তাব। এর সাথে সাথে তাদের ট্রাক্টর, পাম্প, পাওয়ার টিলার ইত্যাদি কেনবার জন্যেও টাকা দেওয়ার প্রস্তাব আসে। তৃতীয় ঘটনাটি এরপর ঘটে। রিচারিয়া ফের বরখাস্ত হয়ে যান। এই সমান্তরাল তিনটি ঘটনাকে, আমার মনে হয়, একসূত্রে গাঁথা যায়। এরপর রিচারিয়া ভারতবর্ষের একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শঙ্কর গুহনিয়োগীর সাহায্য পান। শঙ্কর গুহনিয়োগী তাঁকে মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের আদিবাসীদের মধ্যে থেকে বহুরকমের ধানের ভ্যরাইটির জার্মপ্লাজম সংরক্ষণের একটা সুযোগ করে দেন। এটা আমার লোকমুখে শোনা কথা। পরবর্তীকালে ড. পুণ্যব্রত গুণ-এর সাথে ব্যক্তিগত কথাবার্তায় আমি এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হই। পুণ্যব্রত গুণ আমায় জানান যে তিনি নিজে যখন শহিদ হাসপাতালে ছিলেন, তখন ড. রিচারিয়া সেখানে আসতেন।
এটা হচ্ছে প্রথম দফার গল্প। আসা যাক এর ফলাফলে। এই যে ভারত সরকার দেশীয় ধানগুলো সংরক্ষণের কোনওরকম ব্যবস্থা করল না, এই যে রিচারিয়া-দের মত বিজ্ঞানীদের চরমভাবে হেনস্থার মুখে পড়তে হল, বিভিন্ন বিদেশী জাতকে ভারতবর্ষে ঢোকানো হল, সেগুলির তিনটি নিশ্চিত ফল ফলল। এক নম্বর হচ্ছে, ভারতে এক লক্ষেরও বেশি ধানের ভ্যরাইটি ছিল বলে অনুমান করা হয়, তার থেকে আজ খুঁজলে পাঁচ হাজারটিও আর পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, ধান ও গমখেতে রোগ ও পোকা’র উপদ্রব অস্বাভাবিক রকমের বেড়ে গেল। দু’টি গবেষণার কথা এখানে উল্লেখ করব। একটা হচ্ছে চুঁচুড়া ধান গবেষণা কেন্দ্রের একটি গবেষণা। তাতে দেখা যাচ্ছে তথাকথিত উচ্চফলনশীল ধান যখন পশ্চিমবঙ্গে চাষ করা শুরু হল, তখন থেকে ২৬টি নতুন প্রজাতির প্রাণী নতুন করে ধানের পোকা হিসেবে আবির্ভূত হয়। মানে তাদের আগে কোনও পেস্ট স্ট্যাটাসই ছিল না। এই উচ্চফলনশীল ধান চাষ শুরু হওয়ার পর তারা পেস্ট স্ট্যাটাস পেল। আর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আরেকটি গবেষণায় চোখ রাখলে পাওয়া যাচ্ছে, ধানখেতে ক্ষতিকারক পোকার উপদ্রব ১৯৬৫ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে পাঁচশো শতাংশ বাড়ল। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ল কীটনাশকের ব্যবহার, কীটনাশকজনিত অসুখ ইত্যাদি ইত্যাদি। তার মানে দেশীয় ধানের জাত শেষ হয়ে গেল, রোগপোকার উপদ্রব অস্বাভাবিক রকমের বাড়ল, কীটনাশকজনিত দূষণ বাড়ল। আরও একটা জিনিস হল। যে দেশি জাতকে এককথায় অনুৎপাদক বলে খারিজ করে দিয়ে গ্রিন রেভুলেশন ঢুকলো, তা সংরক্ষণে আমাদের দেশের সরকার কোনও ব্যবস্থা না নিলেও, ইন্টারন্যাশনাল বোর্ড অফ প্ল্যান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস (IBPGR) (ফোর্ড ফাউন্ডেশনের টাকায় পরিচালিত একটি সংস্থা) কিন্তু সেই ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়ে নিল সাগ্রহে। এরা সারা পৃথিবী জুড়ে যতরকমের দেশি জাত আছে গম, ভুট্টা বা ধান তার সংগ্রহ একইসাথে আরম্ভ করল ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশনের সাথে যৌথ উদ্যোগে। তাদের লেটারহেড, খাম ইত্যাদি ব্যবহার করে। ভেবে দেখে নিতে বলবো, ‘দেশী জাত’ মানে কিন্তু কোনও একটি জাত নয়! তার মানে অন্ততপক্ষে এক লক্ষের কাছাকাছি জাত! অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিকভাবে এদের অনুৎপাদক দাগানো হল। কোনও আলাদা আলাদা করে পরীক্ষা এদের নিয়ে হলই না। চুক্তিটা ছিল এরকম যে, বিভিন্ন দেশ থেকে যে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হবে, তার একটা সেট থাকবে IBPGRIBPGR-এর কাছে। আর একটি সেটটা যে দেশ থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে, তাদের কাছে। উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে এরকম ৫,০০০ অতি গুরুত্বপূর্ণ ধানের ভ্যারাইটি সংগ্রহ করা হল এবং এই কাজে IBPGR-কে পুরোমাত্রায় সাহায্য করলেন স্বামীনাথন, কেননা তিনি ছিলেন সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজারি কমিটি টু দ্য ক্যাবিনেট-এর প্রধান এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন গোপন বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে কোথায় কোথায় ওই সমস্ত ধানগুলো পাওয়া যায়। IBPGR এগুলো সংগ্রহ করে নিল এবং তার পরে কিন্তু ভারতকে চুক্তি অনুযায়ী সেটটি দেওয়া হল না। সেটা চলে গেল ফিলিপিন্সে। আজকে যত অমুক পোকা-প্রতিরোধী ধান, তমুক রোগ-প্রতিরোধী ধান, এইসব যা যা উৎপন্ন করা হচ্ছে, সেগুলির মূল জিন ওই সমস্ত জায়গা থেকেই কিন্তু আসছে। মানে আমাদের দেশ থেকে এইভাবে জিনসম্পদ চালান হয়ে গেল। এবং এই কর্মকাণ্ডের জন্যে এম. এস. স্বামীনাথন পুরস্কৃত হলেন এইভাবে যে, তাঁকে IRRI (ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইন্সটিট্যুট) এর ডিরেক্টর করে দেওয়া হল। ভারতের একজন সরকারি বৈজ্ঞানিক যিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গোপন তথ্য জানেন, যিনি খাদ্য নিরাপত্তার গোপনতম তথ্য জানেন, তিনি ফোর্ড ফাউন্ডেশনের টাকায় পরিচালিত IRRI-তে চাকরি করতে চলে গেলেন। আর ভারত সরকার তাঁকে আটকালও না।
এইটাকে আমরা বলতে পারি জিন সাম্রাজ্যবাদের প্রথম পর্যায়। আমাদের দেশ থেকে এইভাবে বহু দুর্মূল্য ভ্যরাইটি অবলুপ্ত হয়ে গেল। এবং, আমাদের দেশের খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা ভীষণভাবে পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ল। এখন ধরুন, যে সমস্ত ভ্যারাইটি ছিল, তার সবগুলোকে নিয়ে তো আমরা কাজ করতে পারছি না। যতটুকু পেয়েছি, যতটুকু জোগাড় করা গেছে সেগুলো নিয়েই আমাদের গবেষণা এবং তা থেকেই চমকপ্রদ ফলাফল। পশ্চিমবঙ্গে এই কাজ প্রথম শুরু করেছিলেন ড. দেবল দেব। আমি সেই সময় তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম। তার পরবর্তীকালে আমি নিজে বেশ কিছু ধানের ভ্যরাইটি সংগ্রহ করি। দেখা গেছে, এখনও এমন কিছু ভ্যারাইটি রয়ে গেছে যেগুলো এম.টি.ইউ ৭০২৯ অর্থাৎ লাল স্বর্ণ বলে যে জাতটা পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি চলছে (তথাকথিত হাই-ইয়েল্ডিং ভ্যরাইটি হিসেবে), তার সাথে ফলনে পাল্লা দিতে পারে কোনওরকম কেমিক্যাল ইনপুট ছাড়াই। আজ এখানে ছবি দেখানোর সুযোগ থাকলে, বহুরূপী এবং কেরালা সুন্দরী নামের যে দুটি ধান আমরা ট্রায়াল দিয়েছি, লাল স্বর্ণর সাথে সেগুলোর তুলনামূলক ফলনের ছবি আমরা দেখাতে পারতাম। এগুলোর সবকটিই হেক্টর প্রতি প্রায় ৪৫-৪৮ কুইন্ট্যাল ফলন দিতে পারে, কোনওরকমের কেমিক্যাল ইনপুট ছাড়াই। এটা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। ফলন নিয়ে যখন কথা হচ্ছে, এখানে আরেকটা তথ্য জানানো দরকার। কেম্ব্রিজ ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া-তে ‘অষ্টাদশ শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতে ধানের ফলন’ সংক্রান্ত কিছু তথ্য আছে। বিভিন্ন শিলালিপি বা এই রকমের অন্যান্য লিপি থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে। বইটির সম্পাদনা করেছিলেন ইরফান হাবিব। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ধানের ফলন প্রতি হেক্টরে ৩.৭ টনের বেশি আকছার হত। আজকে পাঞ্জাবেই এতটা হয় না। আইন-ই-আকবরী থেকে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন জমিতে ধার্য করা খাজনার পরিমাণ। খাজনা ধার্য তো করা হত মোটামুটি জমির গড় ফলন মাথায় রেখে। যেগুলো সবথেকে ভালো জমি, যেখানে সেচের কাজ করা যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি, সেগুলো থেকে ধার্য করা খাজনার দিকে তাকালে মোটামুটি তার ফলন সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়। সেই ফলনে আজকের দিনেও পাঞ্জাব পৌঁছে উঠতে পারেনি, সবুজ বিপ্লবের ছয় দশক পরেও। আমার এক ইতিহাসবিদ্ বন্ধুর ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে এইসব তথ্য যখন আমি সংগ্রহ করছি, তখন আমার উৎসাহ দেখে সেই বন্ধু জানান যে, ওই সময়ের তথ্যের উপর এতটা নির্ভর করাও আবার ঠিক না। কারণ ওই সময় সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এইসব হিসেব সংগ্রহ করা হত না। এটা ঠিক কথাই। কিন্তু আমি নিজে তো চাষ করে দেখছি যে আমার কাছেই এমন দেশি ধান রয়েছে যেগুলো আকছার ৪৮ কুইন্ট্যাল প্রোডাকশন দিয়ে দিচ্ছে প্রতি হেক্টরে। তাহলে ওইসমস্ত তথ্যকে পুরোপুরি অস্বীকারই বা কীভাবে করি! আমাদের দেশে এই যে এত বুভুক্ষা, অপুষ্টি এইসবের পিছনে আমাদের দেশের পশ্চাৎপদ কৃষিপ্রযুক্তি দায়ী — এরকম একটা প্রচলিত ধারণা রয়েছে। এই ধারণার, আমার মনে হয়, একটা পুনর্মূল্যায়ণ প্রয়োজন। কৃষিপ্রযুক্তি নয়, এই বুভুক্ষা বা অপুষ্টির পিছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলোর দিকে এবার বেশি নজর দেওয়া দরকার বলে আমার মনে হয়। আর এটা তো একটা ভয়ানক সত্যি কথা, সবুজ বিপ্লবের ছয় দশক পরেও গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সে ভারতের অবস্থান লজ্জাজনকভাবে খারাপ। উৎপাদন নিয়ে আরও অনেক কথাই বলা যায়। কিন্তু সেই অবকাশ নেই, কারণ আমাদের আলোচনার বিষয় মূলত জিন সাম্রাজ্যবাদ। তো, ঠিক এইভাবেই আমাদের দেশ থেকে জিনসম্পদ বাইরে চলে গেছে। এরপরে দ্বিতীয় পর্যায়ে আসা যাক।
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আবিষ্কারের পর কী হল সেটা আলোচনা করি। এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আবিষ্কারের পরে পরেই কিছু কোম্পানি বহু টাকা খরচা করে বানানো কিছু জেনেটিক্যালি মডিফায়েড ক্রপকে বিভিন্ন দেশে চাষ করানোর চেষ্টা চালাতে লাগল। এই জেনেটিক্যালি মডিফায়েড ক্রপের ভালোমন্দ নিয়ে বলার আগেই দু’চারটি কথা বলার রয়েছে। জেনেটিক্যালি মডিফায়েড কোনওকিছু বানানোর আগে আমরা ধরে নিচ্ছি যে একটা জীবের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্যে একটা বিশেষ জিন দায়ী। সেই জিনটাকে তুলে নিয়ে এসে আমরা অন্য কোনও একটা জীবের মধ্যে যদি ঢুকিয়ে দিই তাহলে ওই বৈশিষ্ট্যটি এই দ্বিতীয় জীবের মধ্যে চলে আসবে। এবং সত্যিই তা আসেও। যেমন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে যে কৌতূহলোদ্দীপক কাজটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে জোনাকি পোকার আলো জ্বলার জন্যে দায়ী যে জিন সেটাকে তুলে এনে তামাক গাছে প্রতিস্থাপন। তার ফলে যে তামাক গাছটি বানানো গিয়েছিল, সেটি একটা হলুদাভ সবুজ আলো বিকিরণ করে। তখন আমাদের ছাত্রজীবন। এই গাছের ছবি বেরিয়েছিল সায়েন্টিফিক আমেরিকান-এ। সেই ছবি দেখব বলে আমরা ইউএসআইএস-এ ঘোরাঘুরি করতাম। মানে জেনেটিক্ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড প্রজাতি বানানো সম্ভব। এবং, সেটা যে সব সময় খারাপই হবে, এমনটা বলব না। যেমন ধরুন এটা কাজে লাগিয়ে আমরা একদম পিওর হিউম্যান ইনসুলিন এখন বানাতে পারছি। মানুষের দেহে যে জিন এটা বানায়, সেই জিন মানব দেহকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে উপযুক্ত ব্যাক্টেরিয়ায় তা প্রতিস্থাপন করলে সেই ব্যাক্টেরিয়া পিওর ইনসুলিন ক্ষরণ করছে। এগুলো চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিপ্লব এনেছে বলা যেতে পারে। বা ধরুন কম আণবিক ভর সম্পন্ন হেপারিন, মানে যেটা হার্ট অ্যাটাক হলে দিতে হয় কাউকে বাঁচানোর জন্যে, সেটাও এভাবে বানানো সম্ভব হচ্ছে। মানে ল্যাবেরটরি’র চার দেওয়ালের মধ্যে এই জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করলে কোনও সমস্যা থাকার কথা নয়। সমস্যাটা হচ্ছে, এই জিন-প্রযুক্তিজাত ফসলকে যখন আমি জমিতে অর্থাৎ উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ছাড়ছি, তখন কী হতে পারে, সেটা নিয়ে। এখানে এটা বলা দরকার, একটা জিন-পরিবর্তিত জীব মানে সেটা একটা নতুন প্রজাতির জীব যাকে আমি প্রকৃতিতে ছাড়ছি। এরকম জীব প্রকৃতিতে আগে ছিলই না। এবারে উন্মুক্ত প্রকৃতিতে এটা কেমন আচরণ করবে, সেটা সম্পর্কে আন্দাজ করতে গেলে প্রকৃতির জটিল ইকোসিস্টেম নিয়ে কিছু বলার দরকার আছে। ধরুন আমাদের দেশে কচুরিপানা প্রথম নিয়ে আসা হয়েছিল এর উজ্জ্বল নীলাভ ফুলের জন্যে, এটা দিয়ে উদ্যান সাজানো যাবে অর্থাৎ একটি উদ্যান উদ্ভিদ হিসেবে এটাকে আনা হয়েছিল। যিনি প্রথম এটা এনেছিলেন, তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি যে অর্ধ শতাব্দী যেতে না যেতেই এটা একটা ক্ষতিকারক জলজ আগাছা হিসেবে গোটা ভারতের খাল-বিল-নদী-নালা ছেয়ে ফেলবে। মাছের উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে যখন বিগহেড কার্প-কে আনা হল, তখনও ভাবা যায়নি যে এর ফলে দেশীয় কাতলার বাড় কমে যাবে। এরকম অনেক উদাহরণই আছে। আমি কয়েকটি চিত্তাকর্ষক উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে এই জটিলতাটি কীরকম পর্যায়ের হতে পারে, তা আন্দাজ করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কঙ্গোতে যখন প্রথম শ্বেতাঙ্গদের উপনিবেশ স্থাপিত হল, তখন শ্বেতাঙ্গরা ওই রেন ফরেস্টের দুর্মূল্য সব কাঠ কেটে কঙ্গো নদী দিয়ে ভাসিয়ে সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত নিয়ে যেত আর সেখান থেকে ইউরোপে সেগুলি জাহাজে করে রপ্তানি হত। এই কাঠ ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রধান অসুবিধে ছিল নদীতে জলহস্তীর উপদ্রব। তারা প্রায়ই নৌকো উল্টে দিত বা কাঠ ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া মানুষদের আক্রমণ করত। কঙ্গো নদী অববাহিকা অঞ্চলে এমন কিছু স্থানীয় উপজাতিভুক্ত মানুষ বাস করেন, যাঁরা ওই জলহস্তীদের মাংস খেতেন। কিন্তু তীর ধনুক দিয়ে জলহস্তী শিকার করা খুবই কঠিন কাজ, তাই তাঁরা খুব কম পরিমাণেই জলহস্তী শিকার করতে পারতেন। এবারে নিজেদের কাজে সুবিধে করার জন্য ওই কাঠচালানকারী শ্বেতাঙ্গদের কোম্পানি ওই অববাহিকার সমস্ত স্থানীয় মানুষদের হাতে অত্যাধুনিক রাইফেল তুলে দিল। আর সেই ভীষণ মারণাস্ত্রের দাপটে কিছুদিনের মধ্যেই কঙ্গো নদী জলহস্তী শূন্য হয়ে গেল। এবারে ব্যাপার হচ্ছে, একটা জলহস্তী প্রতিদিন প্রায় ১ কুইন্টাল করে জলজ আগাছা খেয়ে নেয়। তাই জলহস্তী আর না থাকায় অচিরেই গোটা নদী অববাহিকা আগাছায় ঢেকে গিয়ে নৌচলাচল একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু গল্পটা এখানেই শেষ হল না। ওই জলে একরকমের শামুকও ছিল যারা ওই একই জলজ আগাছা খেত। কিন্তু জলহস্তী বেশিরভাগটাই খেয়ে নিত বলে তাদের ভাগে কম পড়ত, তাই এই প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে তাদের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে ছিল অনেক কম। এবারে জলহস্তী আর না থাকার কারণে আগাছা যেমন বাড়ল, প্রতিযোগিতাহীন পরিস্থিতিতে হু হু করে বেড়ে গেল ওই শামুকের সংখ্যা। এই শামুক ছিল সিস্টোসোমিয়াসিস রোগের ভেক্টর, মানে বাহক। ফলত ওখানকার স্থানীয় মানুষেরা এই রোগে আক্রান্ত হতে শুরু করলো আর কঙ্গো নদী অববাহিকা অচিরেই জনশূন্য হয়ে গেল। তার মানে ভাবুন, জলহস্তীর থাকা না থাকার উপরে নির্ভর করছে ওখানে মানুষের বেঁচে থাকা না থাকা। বোঝাই যাচ্ছে একটা ইকোসিস্টেমের জটিলতা কতটা!
আরেকটা উদাহরণ দিই। আমরা জানি নদীতে পলি পড়লে আমরা ড্রেজার দিয়ে সেই পলি পরিষ্কার করি। ইয়েলোস্টোন নদী (উত্তর আমেরিকা) যখন এরকম পলিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, তখন তাকে এইভাবে ড্রেজার দিয়ে পরিষ্কার করা যাচ্ছিল না। কিছু ইকোলজিস্টের পরামর্শে ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কে নেকড়ে আমদানি করা হল। ১৯১২-১৩ সাল নাগাদই ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক থেকে নেকড়েরা অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এবারে নেকড়ে না থাকার কারণে হরিণে ছেয়ে গিয়েছিল ওই ন্যাশনাল পার্ক। তারা ওই নদীর পাড়ে গ্রেজিং করত। কোনও নতুন গাছ জন্মানো মাত্র তাকে খেয়ে নিত। ফলে কোনও গাছই ওই নদীপাড়ে বাড়তে পারত না। তাই ব্যাপক ভূমিক্ষয় হত আর সেই মাটিই নদীতে নেমে গিয়ে নদীতে পলি তৈরি করে তাকে মজিয়ে দিত। নেকড়েরা ফের ফেরৎ আসার কারণে হরিণ নদীপাড় থেকে সরে উচ্চ অরণ্যভূমিতে চলে গেল। ফলে সেই জায়গায় ঘাস জন্মালো ফের। ইঁদুর এল, খরগোশ এল। তাদের খাওয়ার জন্যে শিয়াল এল, বাজপাখি এল। বড় গাছ জন্মালো। ভূমিক্ষয় কমে গেল। বিভার-রা সেই গাছের গুঁড়ি কেটে কেটে বাসা বানাতে শুরু করলো। সেই বাসার নীচে বাস করতে শুরু করলো অন্যান্য উভচরেরা। আস্তে আস্তে সত্তর বছরের মধ্যে ইয়েলোস্টোন নদী ফের স্রোতস্বিনী হয়ে উঠলো। মানুষ কিন্তু ওখানে প্রায়ই উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হরিণ মারতো, কিন্তু সেটা নেকড়েদের পালন করা ইকোলজিক্যাল রোল-এর কাছে পৌঁছোতে পারেনি। তার মানে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি এই ইকোসিস্টেম একটা ভীষণ জটিল সিস্টেম। এবারে সমস্যাটা হচ্ছে, একটা সিস্টেম যখন খুবই কমপ্লেক্স হয়, তখন তার কোনও একটা জায়গায় যদি আমি একটা ছোট বা বড় পরিবর্তন করি, তাহলে সেটা আখেরে গিয়ে কীরকম জায়গায় দাঁড়াবে সেটা অঙ্ক কষে বলা সম্ভব হয় না। যে কারণেই এক মাস আগে থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া যায় না। আমাদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে যন্ত্রপাতি নেই বলে যায় না, এমনটা নয়। যায় না এ কারণে যে আমাদের গণিত ওই জায়গায় এখনও পৌঁছতে পারেনি বা গণিতের সীমাবদ্ধতাই রয়েছে ওই জায়গায় পৌঁছনোর ক্ষেত্রে। আমি গণিতজ্ঞ নই। তাই ক্যাওস থিয়োরি নিয়ে কিছু বলা আমার ধৃষ্টতা। এটুকু বলতে পারি যে, ভীষণ কমপ্লেক্স সিস্টেমের কোনও একটা অংশে পরিবর্তন আনলে সেটার শেষমেশ ফলাফল পুরোপুরি বলা সম্ভব নয়। এইটাই জেনেটিক্যালি মডিফায়েড ক্রপকে কৃষিক্ষেত্রে আনার ব্যাপারে সবথেকে আপত্তির জায়গা। এই সংক্রান্ত দুচারটে উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও সহজ হবে।
ধরুন বি.টি. তুলো। বি.টি. তুলো আনার সময় বলা হল এটা সব পোকা মেরে দেবে। বিজ্ঞাপনে যেভাবে মিথ্যা বলা হয়, যেমন কমপ্ল্যান খেলে নাকি স্মৃতিশক্তি বাড়ে, তেমন এটাতেও মিথ্যে বলা হল। কিন্তু কিছুটা তো সত্যি হতেও পারে। যেমন পিঙ্ক বোলওয়ার্ম নামে একটা পোকাকে মারতে পারে। আসলে বিটি ফসলের কোষে এমন এক বা একাধিক প্রোটিন তৈরি হয় যা লেপিডেপ্টোরা গোত্রের পতঙ্গকেই মারতে পারে। পিঙ্ক বোলওয়ার্ম এই গোত্রের পতঙ্গ। ফলে পিঙ্ক বোলওয়ার্ম যদি বিটি তুলো গাছের কোনো অংশ খায় সে মারা যাবে। পিঙ্ক বোলওয়ার্ম একটি মেজর পেস্ট। তাই তাকে মারতে বিটি তুলো চাষের অনুমোদন দেওয়া হল। চাষি কোনোরকম কীটনাশক না দিয়ে এই তুলো চাষ করল। স্বাভাবিকভাবেই পিঙ্ক বোলওয়ার্ম মারা গেল। এর ফলে অন্য যেসব মাইনর পেস্ট ছিল, যেগুলো লেপিডেপ্টোরা গোত্রের নয়, যেমন সাদা মাছি, জাব পোকা — সেগুলো মরল না। আর তাদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় তারা এতটাই দ্রুত বেড়ে গেল যে চাষি পরে আর কীটনাশক দিয়েও ফসল বাঁচাতে পারল না এবং আত্মহত্যা করল।
নানান উদ্ভট সব থিয়োরি হাজির হল — চাষিরা ঋণের জন্য আত্মহত্যা করেছেন; বিটি ফসলের আগে থেকেই আত্মহত্যা জারি ছিল কিংবা বিটি তুলোর সাথে চাষিদের আত্মহত্যার সরাসরি কোনো যোগ নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এসবের ফলে তো ফসল উজাড় হয়ে যাওয়া আর সেই চাষিদের আত্মহত্যার ঘটনাটা মিথ্যে হয়ে যায় না। ভুল হতেই পারে। ধরা যাক ভুলই হয়েছিল। মনস্যান্টো কোম্পানি বলে দিতে ভুলে গিয়েছিল যে বিটি তুলো সাদা মাছি মারতে পারে না। তো সেই ভুলের মাসুল দিতে মনস্যান্টো কোম্পানির উচিত ছিল চাষিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া। কিন্তু সেই দাবিটা আমাদের রাষ্ট্র কোনওদিন করতে পারবে না। সেই ধক নেই আমাদের রাষ্ট্রের।
এরপর এক পপুলার সায়েন্স পত্রিকায় দীপক পেন্টাল লিখলেন সব এক্সপেরিমেন্টেরই কিছু ড্রব্যাকস্ থাকে, বিটি তুলো সাদা মাছি মারতে পারে না কিন্তু পিঙ্ক বোলওয়ার্ম মেরেছে, ফলে তুলোর ফলন বেড়েছে। এখন মজার ব্যাপার হল বিটি তুলোর সাথে কিন্তু ফলনের কোনো সম্পর্ক নেই। সার জল ঠিকঠাক দিলে সাধারণ তুলোর ফলনও ভালো হবে। আর আমাকে যদি কীটনাশক দিতেই হবে তাহলে আমি বিটি ফসল ব্যবহার করব কেন? একটা যুক্তি হল বিটি ফসল কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়েছে। কিন্তু উল্টোদিকে আমি তো বিষটাকে তুলোগাছের কোষে কোষে তৈরি করে নিতে দিয়েছি। তুলো তুলে নেওয়ার পর গাছটা যে পড়ে থাকবে তার কি হবে? সেটার তো কোষে কোষে বিষ। সেই গাছটা পচবে, মাটিতে জলে মিশবে। জলে গিয়ে এই বিটি বিষ যে জলজ বাস্তুতন্ত্রের ভয়ানক ক্ষতি করে সেটা রোজি মার্শাল গবেষণা করে দেখিয়েছেন। তাহলে বিষ ব্যবহার করার যা সমস্যা বিটি ফসলের ক্ষেত্রেও সেই একই সমস্যা। আরো সমস্যা হল পোকারা খুব দ্রুত বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে নিতে পারে। র্যাচেল কারসনের লেখা বিখ্যাত বই ‘দি সাইলেন্ট স্প্রিং’ থেকে জানতে পারছি যে ১৯৮৫ সালের মধ্যেই প্রায় সাড়ে চারশো রকমের পোকা বিভিন্ন বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী হয়ে উঠেছিল। তাহলে বিটি বিষ কি এর আওতার বাইরে? ড. টাবাসনিক ল্যাবেরটোরিতে গবেষণা করে দেখালেন যে পিঙ্ক বোলওয়ার্ম কীভাবে খুব দ্রুত বিটি-র দুটো বিষ প্রোটিনের (Cry 1Ac, Cry 2Ab) বিরুদ্ধে যথাক্রমে ২৪০ এবং ৪২০ গুণ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করেছে। তাহলে এত কাণ্ড করে কী পাব আমরা? চাষির মৃত্যু, জলজ ইকোসিস্টেমের ক্ষতি, রাসায়নিক কীটনাশক? কারণ বিটি ফসল তো কয়েক বছরের মধ্যেই আর পোকা আটকাতে পারবে না। সেই বিষ হজম করতে শিখে ফেলা পোকাগুলো তখন হয়ে যাবে সুপার পেস্ট।
আর মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর কী প্রভাব এই বিটি বিষের? আজকালকার স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞান বইগুলোতে রয়েছে যে মানুষের পাকস্থলীতে এই বিটি প্রোটিন নষ্ট হয়ে যায় মাত্র ১৫ সেকেন্ডে। ফলে মানুষের শরীরে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু এর উলটো দিকের গবেষণার তথ্যে (একটি সম্মানীয় বিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকা “রিপ্রোডাকটিভ টক্সিকোলজি” তে ছাপা কানাডার শেরব্রুক ইউনিভার্সিটির এস লেভল্যান্ক ও আব্দুল আজিজ নামে দুই চিকিৎসক-গবেষকের একটি গবেষণাপত্রে পাওয়া যাচ্ছে যে কানাডার এক হাসপাতালে ৯৩% মায়েদের ও ৮০% গর্ভস্থ ভ্রূণের রক্তে রয়েছে এই বিটি বিষ যা অ্যালার্জি, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি করতে পারে। কানাডায় বিটি ফসল অবাধে চাষ হয়। তাহলে বিটি ফসল চাষের পক্ষে মূল যে যুক্তি পরিবেশবান্ধবতা, তার কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিটি ফসল চাষ হবে, বিটি বেগুন, বিটি ঢেঁড়শ, বিটি তুলো, ধান, সরষের চাষ হবে।
এখানে একটা সমস্যাও আছে। জেনেটিক্যালি মডিফায়েড অরগ্যানিজমের ব্যবহার পরিবেশে বা মানবদেহে কী প্রভাব ফেলছে তার গবেষণা করা দিন দিন কঠিনতর হয়ে উঠছে। যেমন ধরুন সায়েন্টিফিক অ্যামেরিকান পত্রিকায় ২৬ জন গবেষক মিলিতভাবে একটি চিঠি পাঠান। সেটাই ওই কাগজের এডিটোরিয়ালে ছাপা হয়। তাতে তাঁরা বলেন জিন পরিবর্তিত ফসলের প্রভাব সংক্রান্ত কোনও গবেষণার কাজ প্রকাশিত হবে কি হবে না তা নির্ভর করে ওই জিন পরিবর্তিত ফসল যারা বানাচ্ছেন সেইসব কোম্পানিগুলোর ইচ্ছের ওপরে। ডেবিড স্কুবার্ট নামে একজন আমেরিকান গবেষক (স্যাল্ক ইনস্টিটিউট) যিনি সেল ও নিউরো বায়োলজির ওপর কাজ করেন, জানিয়েছেন আমেরিকায় জিন পরিবর্তিত ফসলের ছাড়পত্র দেয় যে দপ্তর তারা একটি রাবার স্ট্যাম্প মাত্র, তারা প্রায় চোখ বুজে জিএমও উৎপাদক কোম্পানিগুলির দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে। আমি এরকম আরো অন্তত হাফডজন গবেষকের নাম এক্ষুনি বলতে পারি যাঁরা জিন পরিবর্তিত ফসলের প্রভাবের ওপর কাজ করতে গিয়ে সেগুলোর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাবের কথা বলেছেন। এবং বলার পরেই তাঁদের নানাভাবে হেনস্থা হতে হয়েছে। আর্পাড পুশতাই, রাওয়েট রিসার্চ ইন্সটিট্যুটের গবেষক, জিএম আলু ইঁদুরকে খাইয়ে দেখেছেন ইঁদুরের ক্ষুদ্রান্তের এপিথেলিয়াম কোষে এই আলু ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে ও ইঁদুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে। এটি একটি টিভি সাক্ষাৎকারে বললেন তিনি এবং বলার পরেই তাঁর মতো একজন অত্যন্ত সম্মানীয় গবেষক সম্পর্কে রটানো হল যে, তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে এবং তিনি নাকি ভুল স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড ব্যবহার করেছেন। তখন তিনি বিশ্বের বিভিন্ন জায়গার তাঁর গবেষক বন্ধুদের এই গবেষণার সব তথ্য-পদ্ধতি যাচাই করতে পাঠালেন। প্রত্যাশিতভাবে তাঁরা সকলেই আর্পাড পুশতাইয়ের গবেষণাকেই সমর্থন জানালেন। এরপর ল্যানসেট নামে খুব প্রসিদ্ধ (বলা হয় নেচার পত্রিকার পরেই এর স্থান) একটি বিজ্ঞান পত্রিকায় তাঁর গবেষণাপত্রটি ছাপা হয়। প্রসঙ্গত, দ্য ইকোলজিস্ট পত্রিকায় খুব সুন্দর একটি কার্টুন ছাপা হয়েছিল যার হেডিং ছিল ইভল্যুশন অফ সায়েন্স। ছবিটা এরকম— দুটো পাশাপাশি ছবির একটাতে গ্যালিলিও, তাঁর সামনে পোপ দাঁড়িয়ে। পোপ গ্যালিলিওকে বলছেন যে তুমি যদি চার্চের ডগমা না মানো তাহলে তোমাকে পুড়িয়ে মারব। পরের ছবিতে পোপের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কর্পোরেট বস, আর গ্যালিলিওরূপী পুশতাইকে সে বলছে যে, তুমি যদি কর্পোরেট ডগমা না মানো তা হলে তোমাকে মামলা করে সর্বস্বান্ত করে দেব। এই হাস্যকর অথচ ভয়ঙ্কর বিবর্তনটা বিজ্ঞানের কিন্তু হয়েছে। যতগুলো নাম আমরা পাচ্ছি (রোজি মার্শেল, ইগন্যাশিও চ্যাপেলা) যাঁরা এই জিনগত পরিবর্তিত ফসল নিয়ে কাজ করেছেন এবং এর ক্ষতির দিকগুলো তুলে ধরেছেন তাঁদের সবাইকেই নানাভাবে হেনস্থা হতে হয়েছে।
আরেকটা কথা জিন পরিবর্তিত ফসল নিয়ে বলা যায়। সেটা খানিকটা টেকনিক্যাল বিষয় যদিও। গত শতাব্দীর শেষদিক পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে একটা জিন — সেখান থেকে একটা আরএনএ তৈরি হবে — সেখান থেকে একটা প্রোটিন তৈরি হবে। এমন একাধিক প্রোটিন মিলে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য গঠন করবে। অর্থাৎ জিন থেকে তথ্যের প্রবাহ কেবল একমুখী। কিন্তু এই শতাব্দীর শুরু থেকেই এই ধারণাটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে গেছে। যেমন বিখ্যাত বিজ্ঞানী শ্যাপি্রো, যিনি নোবেল লরিয়েট বিজ্ঞানী বারবারা ম্যাক্লিন্টকের ছাত্র, একটা গবেষণাপত্র লিখেছেন রিভিজিটিং সেন্ট্রাল ডগমা শিরোনামে। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে জিন থেকে প্রোটিনে তথ্যের প্রবাহ একমুখী নয়, এর উল্টোটাও হতে পারে, পরিবেশের প্রভাবে কোনো কোনো প্রোটিন কোনো বিশেষ জিনের আচরনে পরিবর্তন আনতে পারে। অন্যত্র একটা মেটাফর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যদি আমরা একটা বিশেষ সার্কিটের নির্দিষ্ট কাজ করা একটা আইসি চিপ তুলে সেটাকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা সার্কিটে বসাই সেই একই কাজ করার জন্য তাহলে কখনোই কাঙ্ক্ষিত ফল পাব না এবং সেই আইসি-টাও অন্য আচরণ করবে। জিনের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। জন ফ্যাগান আরেক বিজ্ঞানী যিনি আমেরিকার ন্যাশানাল ইন্সটিটিউট অব হেলথ-এর ১.২৫মিলিয়ন ডলারের সরকারি প্রোজেক্ট প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমন আরেকজনও এই একই কথা বলেছেন যে, এভাবে আমরা কখনোই একটা জিন একটা বৈশিষ্ট্য বহন করে এমন কথা বলতে পারি না, এই পুরো ব্যাপারটাই অত্যন্ত জটিল, এবং কয়েক প্রজন্ম পরে সেই জিন কী আচরণ করবে কোনওভাবেই সেটা পুরোপুরি বলা যায় না।
কিছু আইন এমন আসছে যাতে এই সব প্রযুক্তির বিরুদ্ধে বললে বা কোনো প্রমাণ ছাড়া বললে বিরাট অঙ্কের জরিমানা-জেল হতে পারে। এগুলো কি কিছু নির্দেশ করছে না? বোঝাই তো যাচ্ছে যে এসব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের চেয়েও বড় কোনো লবি কাজ করছে। আরেকটা কথা বলে শেষ করব যে গোটা ইউরোপীয় ইউনিয়ন জিএম ফসল ব্যবহার করে না। তাহলে আমাদের রাষ্ট্র যদি এমন যুক্তি দেয় যে, আমরা যেহেতু ডব্লিউটিও-তে সই করেছি তাই এই প্রযুক্তি না মেনে উপায় নেই তাহলে সেটা পরিষ্কার মিথ্যে কথা। কারণ কার্টেজিনা প্রোটোকলে পরিষ্কার বলা আছে যদি কোনো দেশ নৈতিকতার কারণে কিংবা তার উপভোক্তাদের অপছন্দের কারণে জিএ্ম শস্য ব্যবহারে অসম্মত হয় তাহলে সেটা কখনোই ডব্লটিও আইনের পরিপন্থী হবে না।
কিন্তু ভারত সরকারের চরিত্র আমরা জানি, সে কী করে আর কাদের স্বার্থরক্ষা করে তাও জানি। তাই বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড ফসল চাষ বন্ধ হবে এমন কোনো আশা আছে বলে আমি মনে করি না। যদি না আমরা নিজেরা ময়দানে নেমে এটাকে প্রতিরোধ করি।
লেখক স্বাধীন ধান গবেষক ও সংরক্ষক। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে দেশী ধান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে তিনি ছ’শরও বেশি ধান সংরক্ষণ করেছেন। এছাড়া ধানের আণবিক জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা পত্র তার আছে। তিনি ধান ক্ষেতের বাস্তুতন্ত্র নিয়েও গবেষণা করেছেন এবং গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছেন।
The article was originally published at https://fiamindia.org/blog


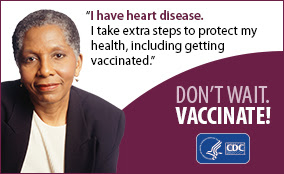
Comments
Post a Comment